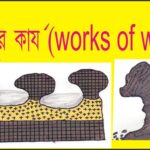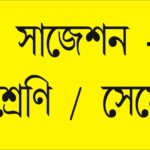হিমবাহ ও গঠিত ভূমিরূপGlacier and associated landforms/XII-3rd Sem
(১) হিমবাহ এক প্রকার বহির্জাত প্রক্রিয়া
(২) উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এবং উচ্চ অক্ষ্যাংশের (80⁰-90⁰) শীতল জলবায়ু অঞ্চলে হিমবাহের কাজ বেশি দেখা যায়।
(৩) ইংরেজি শব্দ Glacier শব্দটি ফরাসি শব্দ Glace (বরফ) অথবা ল্যাটিন শব্দ Glacies থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
(৪) হিমবাহ হল বরফের নদী। ধীরগতিসম্পন্ন গতিশীল বরফের স্তূপকে বা বরফের চাঁইকে হিমবাহ বলে।
(৫) হিমবাহের উৎপত্তি :- নেভে, ফার্ন, বরফ এই তিনটি পর্যায়ে হিমবাহের উৎপাত ঘটে।
(৬) নেভে (Neve) :- উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ও উচ্চ অক্ষ্যাংশে বৃষ্টিপাতের বদলে তুষারপাত হয়।এই তুষারপাতের ফলে যে দানাকৃতি তুষারখন্ড সৃষ্টি হয় তাকে নেভে বলে। নেভের আকৃতি 0.06-0.16 গ্রাম/ঘনসেমি হয়।
(৭) ফার্ন (Firn): নেভে পরস্পরের সঙ্গে জমাট বেঁধে কঠিন কেলাসে পরিণত হলে তাকে ফার্ণ বলে।
ফার্ণের ঘনত্ব 0.72-0.84 গ্রাম/ঘনসেমি
বরফ (ICE) :- ফার্ণ পরস্পরের সঙ্গে জমাট বাঁধলে যে কঠিন তুষার পিন্ডের সৃষ্টি হয় তাকে বরফ বলে, বরফের ঘনত্ব 0.918 গ্ৰাম/ঘনসেমি।
(৮) হিমবাহ :- মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বরফের স্তূপ বা বরফের চাঁই ধীরগতিতে প্রবাহিত হলে হিমবাহ বলে।
(৯) হিমরেখা (Snowline) :-
যে কাল্পনিক সীমারেখার উপারে তুষার জমে বরফে পরিণত হয় কিংবা যে কাল্পনিক সীমারেখার নিচে বরফ জলে পরিণত হয় তাকে হিমরেখা বলে। হিমারখারা উচ্চতা সর্বত্র সমান নয়। উচ্চ অক্ষাংশে হিমরেখার উচ্চতা কম এবং নিম্ন অক্ষাংশে হিমরেখার উচ্চতা বেশি। হিমালয়ে হিমরেখার অবস্থান দেখা যায় 3800-4800 মিটার উচ্চতায় গ্রীষ্মকালে হিমরেখার উচ্চতা বেশি তার শীতকালে হিমরেখার উচ্চতা কম।
অক্ষাংশ ——————– হিমরেখার অবস্থান
90⁰ ————– 100মিটার বা সমুদ্রতলের প্রায় সমান
80⁰ —————– 1000 মিটার
70⁰ ————– 1200 মিটার
60⁰ ————– 1500 মিটার
50⁰ ————— 1800 মিটার
40⁰ ————— 3000 মিটার
30⁰ ————— 3500 মিটার
23½⁰ ————– 4500 মিটার
0⁰ ——————- 6000 মিটার
201
(১০) হিমরেখার বৈশিষ্ট্য :-
(১) হিমরেখার উচ্চতা নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে, মেরুর দিকে ক্রমশ কমতে থাকে।
(২) হিমরেখার উপর চির তুষার ক্ষেত্র বিরাজ করে।
(১১) হিমরেখার নিয়ন্ত্রক :- হিমারেখার অবস্থান ও উচ্চতা যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তাদের হিমরেখার নিয়ন্ত্রক বলে। এগুলি হল-অক্ষাংশ, উচ্চতা, ভূমির ঢাল, ঋতু , জ্বলীয় বাস্প, বায়ুপ্রবাহ, জলবায়ু ।
(১২) হিমরেখার প্রকারভেদ :- হিমরেখা দুই ধরনের হয় – (i) স্থায়ী হিমরেখা
(ii) অস্থায়ী হিমরেখা
স্থায়ী হিমরেখা :- যে উচ্চতার উর্দ্ধে বরফ কখনই গলে না তাকে স্থায়ী হিমরেখা বলে।
অস্থায়ী হিমরেখা :- যখন হিমরেখার উচ্চতা, অক্ষাংশ, ঋতু ভেদে পরিবর্তন হয় তখন তাকে অস্থায়ী হিমরেখা বলে।
হিমবাহের শ্রেনিবিভাগ (classification of glacier)
১৯৪৮ সালে বিখ্যাত হিমবাহ বিশেষজ্ঞ অ্যলমান(Ahlman) তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন।
(1) পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ (mountain or valley) :- উচ্চ পর্বত বা উপত্যকায় সৃষ্ঠ হিমবাহকে পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ বলে । এই হিমবাহ পর্বতের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে।
বৈশিষ্ট্য : (I) হিমরেখা অতিক্রম করলে এই হিমবাহ (পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ) থেকে নদ নদী সৃষ্টি হয়।
(II) বার্গশ্রুন্ড ও ক্রেভাস দেখা যায়।
(III) এই হিমবাহের মধ্যভাগ অবতল প্রকৃতির হয় ।
(IV)হিমবাহের আকৃতি খুব বড় হয় না।
উদাহরণ :- (১) আলাস্কার হুবার্ড পৃথিবীর বৃহত্তম পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ। এর দৈর্ঘ্য ১২২ কিমি এবং প্রস্থ ১০ কি.মি।
(২) ভারতের কারাকোরাম পর্বতের সিয়াচেন হিমবাহ ভারতে দীর্ঘতম উপত্যকা হিমবাহ এর দৈর্ঘ্য ৭৬ কিমি।
(৩) অন্যান্য হিমবাহ :- (I) হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ দৈর্ঘ্য ৩০কিমি, প্রস্থ ২-৪ কিমি।
(১) মহাদেশীয় হিমবাহ :-
উচ্চ অক্ষাংশে উভয় মেরু অঞ্চলে বিশাল এলাকা জুড়ে যে বরফ স্তূপ দেখা যায় তাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে।
বৈশিষ্টঃ (১) মহাদেশীয় হিমবাহের আয়তন খুব বড়।
(২) মহাদেশীয় হিমবাহ দেখতে অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো বা উল্টানো চামচের মতো।
(৩) মহাদেশীয় হিমবাহের গভীরতা খুব বেশি (প্রায় 250 – 3000 মিটার।
(8) নুনাটাক বা নুনাটক (বরফমুক্ত পর্বত শিখর) দেখা যায়।
(৫) হিমশৈলের সৃষ্টি হয়।
(৬) পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের 10% এলাকাজুড়ে মহাদেশীয় হিমবাহ অবস্থান করে আছে।
উদাহরণ :- (ক) অ্যান্টার্কটিকার ল্যাম্বার্ট বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশীয় হিমবাহ দৈর্ঘ্য 402 কি-মি এবং প্রস্থ 80 কি মি গভীরতা 2000- 2500 মিটার।স
হিমবাহ সংক্রান্ত কিছু তথ্য-
হিমশৈল (Ice berg) : – সমদ্রজলে ভাসমান পাহাড় প্রমাণ বরফস্তূপকে হিমশৈল বলে।
উৎপত্তিঃ মহাদেশীয় হিমবাহ প্রসারিত হয়ে
সমুদ্রের নিকটে চলে আসে এরা সমুদ্র খোজ ও তাপের ধাক্কায় হিমবাহের প্রান্ত ভাগ ভেঙে গিয়ে জলে ভাসতে থাকে।
বৈশিষ্ট্য: (ক) হিমাশৈলের ⅑ অংশ জলের উপরে ভেসে থাকে।
(খ) হিমশৈল বাহিত বিভিন্ন পদার্থ মগ্নচড়া সৃষ্টি করে।
(গ) হিমশৈলের আঘাতে জাহাজ, নৌকা স্টিমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
(ঘ) 1912 সালে টাইটানিক জাহাজ হিমশৈলের আঘাতে ডুবে যায়।
(২) বার্গস্রুন্ড ও র্যান্ডক্লাফট (Bergshrund and randkluft) :Berg=পর্বত, Schround= ফাউন্ড
উচুঁ পার্বত্য অঞ্চল থেকে উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ যখন পর্বতের পাদদেশে নেমে আসে তখন হিমবাহ ও পর্বত গাত্রের মধ্যে যে ফাটল দেখা যায় তাকে বার্গস্রুন্ড বাল। ফরাসি ভাষায় বার্গস্রুন্ডকে রিমে (Rimaye) বলা হয়।
– বৈশিষ্ট্য :
(I) সার্কের মস্তক প্রাচীরের নিকট বার্গস্রুন্ড গঠিত হয়।
(II) হিমবাহের পৃষ্ঠভাগ থোক পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।
(III) গভীরতা 100 – 150 মিটার হয়।
(IV) হিমবাহ পুরু বেশি হলে বার্গস্রুন্ডের গভীরতা বাড়ে।
(V) গ্রীষ্মকালে দৃষ্টিগোচর হয়। অন্য ঋতুতে হাল্কা তুষার দ্বারা ঢাকা থাকে।
উদাহরণঃ (I) নেপালের লোৎসে পর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে দেখা যায়।
(II) এভারেস্টের খুম্বু হিমবাহে বার্গস্রুন্ড দৃষ্টিগোচর হয়।
র্যান্ডক্লাফট (Randkluft):– বার্গস্রুন্ড সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে সার্ক হিমবাহ ও পর্বতগাত্রের মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয় তাকে র্যান্ডক্লাফট বলে।
বৈশিষ্ট্যঃ (I) এগুলি পর্বতগাত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয় না।
(II)হিমবাহ ও সার্কের মস্তক প্রাচীরের মাঝে র্যান্ডক্লাফট দেখা যায়।
(III)র্যান্ডক্লাফট তুষারে ঢাকা থাকে বলে পর্বতারোহীদের কাছে মরণফাঁদ হিসেবে অবস্থান করে।
উদাহরণঃ ইউরোপের আল্পস পর্বতের ব্লুইজ বা ব্লাউইজ (Blaueis) হিমবাহে র্যান্ডক্লাফ দেখা যায়।
ক্রিভাস বা ক্রেভাস (crevas) কী?
খাড়া ঢালের মধ্য দিয়ে চলমান হিমবাহের বিভিন্ন অংশে বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের কারণে যে আড়াগাড়ি উল্লম্ব ফাটলের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিভাস বা। ক্রভাস বলে।
বৈশিষ্ট্য: (1) এগুলির গভীরতা 15-50 মিটার হয়।
(II) ঢাল খুব খাড়া হয়।
(III) হাল্কা তুষার দ্বারা আবৃত থাকে।
উদাহরণ:- আলাস্কার কেন্নিকট হিমবাহে ক্রিভাস দেখা যায়।
(১) হিমবাহের গতি – হিমবাহ অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন প্রাকৃতিক শক্তি। হিমবাহের গড় গতিবেগ বছরে 5-30 মিটার। হিমালয়ে এর গতিবেগ দৈনিক ।-2 সে.মি আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের গতিবেগ’ প্রতিদিন 5-6 সেমি।
(২) পৃথিবীর দ্রুততম হিমবাহঃ গ্রীনল্যান্ডের জেকভসবন বা জেকোভসান (Jakobshavn) ইস ব্রায়ে। এর গতিবেগ বছরে 17 কি মিঃ।
(৩) স্নাডট (snout): প্রবহমান হিমবাহের মধ্যভাগ পার্শ্বভাগ অপেক্ষা দ্রুত অগ্রসর হলে হিমবাহের সম্মুখভাগ অনেকটা জিভের মতো এগিয়ে যায়। একে স্নাউট বলে।
(৪) হিমানী সম্প্রপাত (glacier avalanche)– পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিঢালের পার্থক্যহেতু চলমান হিমবাহের কিছু অংশ হঠাৎ ভেঙে প্রবলবেগে নিচের দিকে আছড়ে পড়ে। একে হিমানী সম্প্রপাত বলে। হিমানী সম্প্রপাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাস, জনপদ, কৃষিক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়।
হিমবাহের পশ্চাদপসরণ :- হিমবাহ নামতে নামতে হিমরেখা অতিক্রম করলে এর সামনে দিকটা গলতে আরম্ভ করে এবং হিমবাহের আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হয়। একে হিমবাহের পশ্চাদপসারণ বলে।
(৫) হিমবাহের কাজ: হিমবাহ তিনপ্রকার ফার করে।
(১) ক্ষয়কার্য (২) বহনকার্য (৩) সঞ্চয়কার্য
ক্ষয়কার্য (Erosion): হিমবাহ তিনটি প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কার্য সম্পন্ন করে।
(ক)উৎপাটন (plucking)
(খ) অবঘর্ষ (Abrasion)
(গ) ঘর্ষন (Attrition)
উৎপাটনঃ প্রবহমান হিমবাহের প্রবল চাপে পর্বতগাত্র থেকে শিলাখন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে যায়। এক উৎপাটন বলে।
হিমবাহ যখন প্রবাহিত হয় তখন হিমবাহের কিয়দংশ গলে গিয়ে জলে পরিনত হয়। এই জল শিলার ফাটলে প্রবেশ করলে তা জমে বরফে পরিনত হয় এবং আয়তনে বেড়ে ফাটলে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে শিলাস্তর গতি সহজেই উৎপাটিত হয়।
অবঘর্ষ :- উৎপাটন প্রক্রিয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাখন্ড হিমবাহের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে উপত্যকাকে প্রবল চাপে মসৃণ করে। একে অবঘর্ষ বলে।
ঘর্ষণ :- হিমবাহের ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ পরিবাহিত হবার সময় পরস্পরে রাগাতে ভেঙ্গে ছোটো হয়ে যায়। একে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া বলে।
(৬) হিমবাহের ক্ষয়কার্যের নিয়ন্ত্রক :-
হিমবাহের ক্ষয়কার্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। যেমন-
(ক) গতিবেগ :- হিমবাহ যত গতিবেগ সম্পন্ন হবে ক্ষয়কার্য তত বেশি প্রবল হবে।
(খ) বরফের গভীরতা :- হিমবাহ যত বেশি পুরু হবে তত বেশি চাপ সৃষ্টি করে ক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
(গ) শিলার প্রকৃতি :- শিলার প্রকৃতির উপর হিমবাহের ক্ষয়কার্য নির্ভরশীল। কঠিন শিলাকে হিমবাহ কম ক্ষয় করে এবং কোমল শিলা বেশি পরিমাণে ক্ষয় করতে পারে। যেমন পার্বত্য অঞ্চলে যদি গ্ৰানাইট শিলা বেশি থাকে তার এই অঞ্চল কম ক্ষয়প্তাপ্ত হয়। পাললিক শিলা থাকলে ক্ষয়ের মাত্রা বেড়ে যায়।
(ঘ) হিমবাহের স্থায়িত্ব :- যে অঞ্চলে হিমবাহ যত বেশিদিন স্থায়ী হয় সেই অঞ্চলে ক্ষয়কার্যের পরিমাণ তত বাড়ে
(৭) হিমবাহের বহন কাজ :- হিমবাহ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ হিমবাহের আকর্ষণে পরিবাহিত হতে থাকে। হিমবাহের গায়ে লটকে থাকা পদার্থ যেমন পরিবাহিত হয় তেমনি হিমবাহের গলনের ফলে তার সঙ্গে সূক্ষ্ম পদার্থ মিশে পরিবাহিত হয়।
(৮) হিমবাহের সঞ্চয়কাজ :- হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত
বিভিন্ন আকৃতির পদার্থ প্রবাহপথের যত্রতত্র ওর জমা হতে থাকে। একে হিমবাহের সঞ্চয়ের কাজ বলে।
(৯) হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
(Erosional Land forms of glacier) :-হিমবাহের ক্ষয়কার্য দ্বারা গঠিত ভূমিরূপগুলি হল :-
(I) সার্ক বা করি (cirque or corrie)
(II) সার্ক হ্রদ (cinque Lake)
(III) অ্যারেৎ বা এরিটি (Arete)
(IV) পিরামিড চূড়া (pyramidal peak or glacier horn)
(V) হিমাদ্রোণী বা U-আকৃতির উপত্যকা Glacier trough on U-shaped valley
(VI) ঝুলন্ত উপত্যকক্স Hanging valley
(VII) ফিয়োর্ড (Fiyord)
(VIII) ক্র্যাগ ও টেল (crag and Tail)
(IX) রসে মতানে (Roche moutonnee)
(X) কর্তিত স্পার (Truncted spur)
(XI) প্যাটারনস্টার হ্রদ (paternoster Lake)
(XII) হিমসিঁড়ি (Glacier stairway)
(XIII) কুঁজ বা হোয়েল ব্যাক (Whale back)
(I) সার্ক বা করি :-
উচ্চপাবর্ত্য অঞ্চলে হিমবাহের গতিপথে উৎপাটন ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার দ্বারা হাত ওয়ালা ডেকচেয়ারের মতো যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাক সার্ক বলে।
সার্কের নানা নাম :- ফ্রান্সে-সার্ক আমেরিকা ইংলন্ডে, স্কটল্যান্ডে-করি। জার্মানিতে কার (kar)। নরওয়েতে বন বা বটন (botton) স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় কেদেল বা কিজেলে স্পেনে- হয়ো ।
ওয়েলসে- কাম বা কুম
নামকরণ :- 1823 সালে ফরাসী বিজ্ঞানী শারপেঁতিয়ার (Charpentier) সর্বপ্রথম সার্ক শব্দটি ব্যবহার করেন।
বৈশিষ্ট :- (I) সার্ক দেখতে আরামদায়ক চেয়ারের মতো
(II)সার্কের তিনটি অংশ – ক) খাড়া পশ্চাৎ চাল (মস্তকের দিকে) (খ) মধ্যখানে খাত (গ) প্রান্তভাগ
(III) সার্ক হিমবাহের ক্ষয়জাত ভূমিরূপ
উদাহরণ :- আন্টার্কটিকার ওয়ালকট সার্ক পৃথিবীর বৃহত্তম ও গভীরতম সার্ক বা করি।
এর গভীরতা 3-4কিমি এবং প্রস্থ 16 কিমি ।
(2) সার্ক হ্রদ:-
অনেকসময় সার্কের মধ্যে ছোট ছোট বরফ বা হিমবাহের টুকরো থেকে যায় । পরে এই বরফ টুকরো গলে গেলে সার্ক হ্রদ বা করি হ্রদের সৃষ্টি হয়।
(3) অ্যারেৎ বা এরিটি :-
করি বা সার্কগুলির মস্তক দেশ অবঘর্ষ ক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়িত হয়ে ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। ফলে পাশাশপাশি দুটি করি বা সার্কের মধ্যখানে যে তীক্ষ্ণ প্রাচীর বা হিমশিরা দেখা যায়। অ্যারেৎ বা এরিটি বলে।
বৈশিষ্ঠ্য :- (I)এরিটি দেখতে অনেকটা করাতের দাঁতের মতো হয়।
(II)এর দুটি অংশ – উত্তল ও অবতল।
(III) এরিটি কোনো কারণে ভেঙে গেলে এক সার্ক থেকে অন্য সার্কে যাওয়ার যে পথ সৃষ্টি হয় তাকে সার্ক গিরিপথ বলে।
উদাহরন :- আল্পস পর্বতের ও হিমালয়ের নীলকন্ঠ পর্বতে এরিটি দেখা যায়।
(4) পিরামিড চূড়া (pyramid peak):–
পাশাপাশিতিন-চারটি সার্ক অবস্থান করে থাকলে সার্কগুলির মধ্যবর্তী অংশ পিরামিডের মতো দেখতে হয় ।একে পিরামিড চূড়া বা হর্ণ বলে ।
বৈশিষ্ট্যঃ (I) শীর্ষভাগ খাঁড়া ঢাল বিশিষ্ট হয়।
(II) সার্কের পশ্চাদপ্রসারণের ফলে পিরামিড চূড়ার সৃষ্টি হয়। অথাৎ সার্কের মস্তক ক্ষয় দ্বারা পিরামিড চূড়া গড়ে ওঠে।
(III) পিরামিড চূড়াকে হর্ন (Horn) নামে অভিহিত করা হয় আল্পস পাতের ম্যাটার হর্ন নামানুসারে পিরামিড চূড়াকে হন বলা হয়।
উদাহরণ: (I) নেপালের মাকালু, ভারতের নীলকণ্ঠ সুইজারল্যান্ডের অবস্থিত আল্পস পর্বতের ম্যাটার হর্ন
(II) পিরামিড চূড়া তারা মাছের মতো দেখতে হলে তাদের ‘star fish Aretes” বলা হয়।
(৫) হিমদ্রোণী যা U-আকৃতির উপত্যকা :-
পাবর্ত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে যে U-আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয় তাকে হিমদ্রোনী বলে।
উৎপত্তি :- পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হলে পার্শ্বক্ষয় ও মিম্নক্ষয়ের মাধ্যমে উপত্যকার উভয়পার্শ্ব খাড়া এবং তলদেশ মসৃণ প্রশস্ত আকার ধারণ করে ইংরেজি U- আকারে পরিণত হয়।
বৈশিষ্ট্য :- (১)হিমদ্রোণীতে হিমবাহ গলে হ্রদের সৃষ্টি করে। যেমন- রূপকুণ্ড
(২) U-আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টিতে পার্শ্বক্ষয় ও নিম্নক্ষয় যৌথভাবে কাজ করে।
(৩) হিমদ্রোনীর মধ্যে হিমবাহের ক্ষয়ের ফলে লম্বা এবং গভীর গর্তের সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ লম্বা খাতকে গ্ৰুভস (Grooves) বলা হয়। এক একটি খাত 12 কি.মি লম্বা এবং 100 কিমি গভীর হয়।
উদাহরণ :- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োসেমিতি বা ইয়োসোমাইট (yosomite) একটি U-আকৃতির উপত্যকা।
(৬) ঝুলন্ত উপত্যকা :-
প্রধান হিমবাহের দুপাশ থেকে ছোটো ছোটো উপ-হিমবাহ এসে মিলিত হয়। প্রধান হিমবাহের ক্ষয় শক্তি উপ হিমবাহ অপেক্ষা বেশি হওয়ার জন্য প্রধান হিমবাহ উপত্যকা গভীর হয়। কিন্তু উপ-হিমবাহ উপত্যকা তুলনামূলক ভাবে প্রধান হিমবাহ উপত্যকা অপেক্ষা কম গভীর হওয়ায় সেগুলি যেন প্রধান হিমবাহ উপত্যকার উপর ঝুলছে। এদের ঝুলন্ত উপত্যকা বলে।
বৈশিষ্ট্য :- (I) ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত গঠিত হয়।
(II) হিমাদ্রানী হले নদী উপত্যকার পরিবর্তিত রূপ।
(উদাহরণ :- ভারতের বদ্রীনাথের নিকট ঋষিগঙ্গা উপত্যকা (উত্তরাখন্ড)
(৭) ফিয়োর্ড :
উপকূলবর্তী অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা গভীর হয়। ফলে সমুদ্রের জল এই উপত্যকায় প্রবেশ করে। হিমবাহ দ্বারা সৃষ্ট এরূপ জলমগ্ন হিমবাহ উপত্যকাকে ফিয়োর্ড বলে।
বৈশিষ্ট্য :- (I) হিমবাহের উৎপাটন ও অবর্ঘষ ক্রিয়ার মাধ্যমে ফিয়োর্ড গঠিত হয়।
(II) ফিয়োর্ড দেখতে লম্বাটে বেসিনের মতো।
(III)উচ্চ অক্ষাংশে ফিয়োর্ড বেশি দেখা যায়।
(IV) ক্ষুদ্র আকৃতির ফিয়োর্ডকে ফিয়ার্ড বলে।
উদাহরণ :- নরওয়েকে ফিয়োর্ডের দেশ বলে।
নরওয়ের সোগনে বা সৌভনে পৃথিবীর বৃহত্তম ফিয়োর্ড।
(৮) ক্র্যাগ ও-টেল :-
হিমবাহের গতিপথে যদিকোনো অঞ্চলে কঠিন শিলার পিছনে কোমল শিলা অবস্থান করে, তাহলে কঠিন শিলা হিমবাহের দ্বারা সামান্য পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও কোমল শিলাকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ফলে বৃহৎ ও কঠিন শিলাখন্ড উঁচু ঢিবির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একে ক্র্যাগ বলে। অপরদিকে কোমল শিলা সরু লেজের মতো কঠিন শিলার পিছনে অবস্থান করে। একে টেল বলে।
বৈশিষ্ট্য :- (I) ক্র্যাগ খাড়া ঢাল বিশিষ্ট এবং টেল মৃদুঢাল বিশিষ্ট হয়।
(II) ক্র্যাগ অমসৃন এবং টেল মসৃণ হয়।
(III) টেল 1-2 কিমি লম্বা হয়।
(IV) টেল ক্র্যাগের সঙ্গে প্রায় 30⁰ কোনে অবস্থান করে
উদাহরণ :- স্কটল্যান্ডের এডিনবরা ক্যাসেল
(৯) রসে মতানে :-
1804 সালে ভূ-বিজ্ঞানী সসার (Saussure) সর্বপ্রথম রসে মতানে শব্দটি ব্যবহার করেন হিমবাহের গতিপথে কোনো প্রস্তরখন্ড ঢিবির আকারে অবস্থান করে থাকলে হিমবাহ যেদিক থেকে প্রবাহিত হয়। প্রস্তরখণ্ডের সেই দিকটি অবঘর্ষ ক্রিয়ার দ্বারা মসৃণ হয় এবং বিপরীত পার্শ্ব অমসৃণ তাবস্থায় থাকে। একে রসে মতানে বলে।
বৈশিষ্ট্য :- (I) এটি দেখতে উত্তল আকৃতির ।
(II)এটি দেখতে শয়নরত ভেড়ার মতো। তাই একে মেষপৃষ্ট শিলা বলে।
উদাহরণ :- কাশ্মীরের লিডার নদী উপত্যকায় এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় লাম্বার্ট ডোম নামে রসে মতানে দেখা যায়।
(২২) হিমর্সিড়ি ও প্যাটার নস্টার হ্রদ :-
হিমবাহের বৈষম্যমূলক ক্ষয়কার্যের ফলে পাবর্ত্য উপত্যকায় যে ধাপের সৃষ্টি হয় তাকে হিমসিঁড়ি বলে।
হিমসিঁড়ির ধাপ ভূমিতালের দিকে না হয়ে পর্বতগাত্রের দিকে হলে এই অংশ জল জমে হ্রদের সৃষ্টি করে। এদের প্যাটার নস্টার হ্রদ বলে।